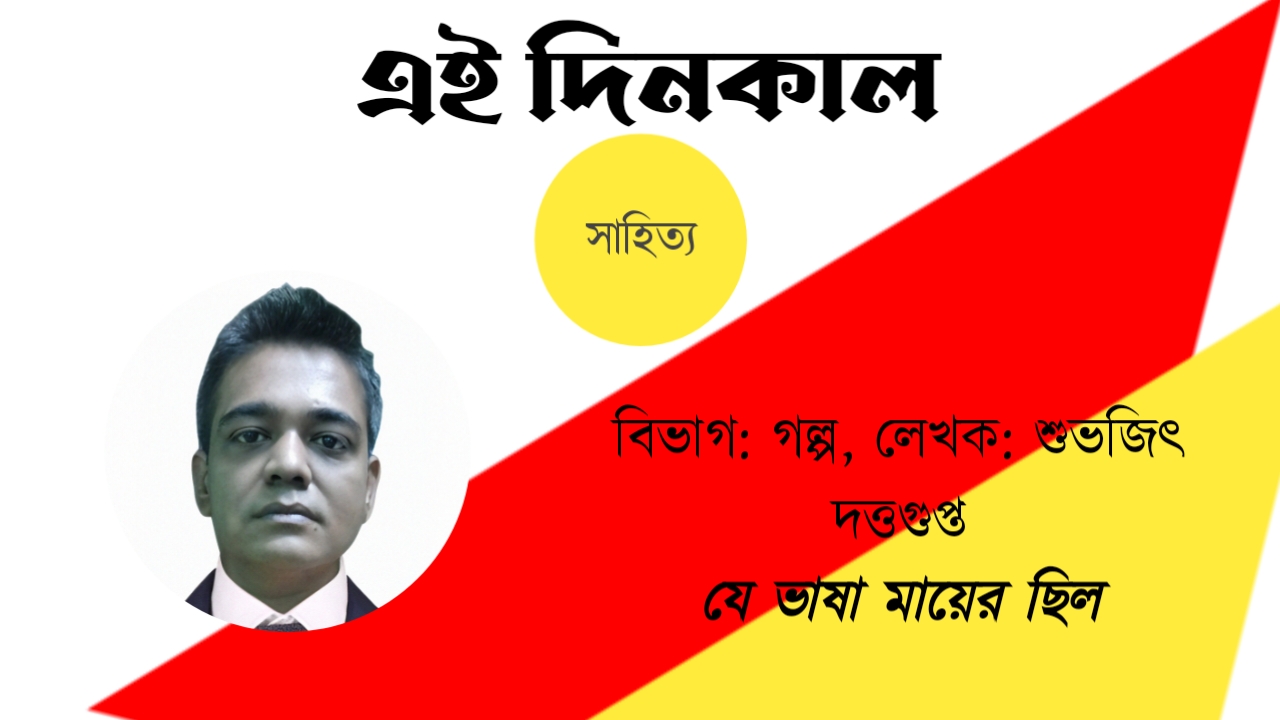শুভজিৎ দত্তগুপ্ত
নবগ্রাম স্টেশন থেকে পঞ্চাশ মিনিট হাঁটলেই এক গ্রাম—বোরোডাঙা। এখন লোকজন চেনে না খুব একটা, কারও কারও কাছে পরিচিত “ওই ক্যানেলের পাড়ের পাড়া” নামে। কিন্তু এক সময় এই পাড়াতেই ছিল বাউলতলা, চড়কমঞ্চ, শখের যাত্রাদল আর জলখেলা-ভাটিয়ালির রেওয়াজ।
সেই পাড়ারই এক মাটির দালানবাড়িতে থাকতেন সুবর্ণা রায়—সবার মুখে “সুবোদি”।
গায়ের গা-লাগা এক অদ্ভুত সুরে কথা বলতেন তিনি, যেটা একদিকে পুরনো রাঢ়বঙ্গীয় উপভাষার ছোঁয়া, অন্যদিকে ব্যক্তিগত আবেগ ও অভ্যাসে গড়া নিজস্ব কণ্ঠসংস্কৃতি। সে ভাষায় ‘পিঠে’ হয় ‘ফিটা’, ‘ছেলে’ হয় ‘ভোবা’, ‘ভাত’ হয় ‘ভোত’—আর এই ভাষায় মা ডাকে যেমন, বকেও তেমন।
তাঁর ছেলে অভিমন্যুর ডাকনাম ছিল সেই টানেই—ভোবা।
সুবর্ণার মুখে এই ভাষাই ছিল ভালোবাসার কণ্ঠস্বর। তিনি বলতেন,
“ভোবা আয় রে, গরুর গোয়াল থেকে দুধ আনবি, মা ভাত গরম করে রাখছি।”
অভিমন্যু বড় হতে হতে শহরের স্কুলে ভর্তি হল। সেখানে শিক্ষক বলতেন, “শুদ্ধ বাংলা চর্চা করো, গ্রাম্য টান বাদ দাও।”
একদিন স্কুল থেকে ফিরে ছেলে মাকে বলল, “তুমি এমনভাবে বলো না তো মা, সবাই হাসাহাসি করে।”
সুবর্ণা মুচকি হেসে বলেছিলেন, “তুই যেমন আমাকে ডাকিস, সেই ডাকটাই তো আমি তোকে দিয়েছিলাম রে। এখন তুই ভুলে গেলি, আমি তো পারলাম না।”
তবে অভিমন্যু ভুলে গেল। উচ্চশিক্ষা, বড় চাকরি, মহানগর—সব মিলিয়ে তার ভাষা পাল্টে গেল, তার টান পাল্টে গেল, এমনকি তার নামও—অভিমন্যু হয়ে উঠল ‘অভি’।
সুবর্ণা থেকে গেলেন গ্রামে—পুরনো পাটকাঠির বিছানায়, খুপরি জানালার ধারে, যেখানে শিউলি গাছ থেকে রোজ ঝরে পড়ত সকালের সাদা রোদ।
দিন গড়াল। বছর পেরোল। ছেলের ব্যাঙ্গালোরে চাকরি, বিয়েশাদি, সংসার। মায়ের সঙ্গে ফোনে বাংলা নয়, ইংরেজি বা ‘নির্জীব শহুরে কথা’।
কিন্তু সুবর্ণা কথা বলে যেতেন নিজের ভাষায়। কারও সঙ্গে না হোক, নিজের সঙ্গেই—এক খাতা ভরে উঠত তাঁর লেখায়—
“ভোবা, তুই ফিরে আসবি তো? এই মাটির গন্ধ তোকে ডাকবেই—ফিটায় রোদ পড়েছে, গোয়ালে গরু দুধে ভেসে গেছে…”
যখন অসুস্থ হলেন সুবর্ণা, তখনো ছেলে এল না। অফিসের চাপ, মেয়ের টেস্ট, ফ্লাইট পাওয়া যায়নি।
একদিন প্রাইমারি স্কুলের দিদিমণির হাতে একটি চিঠি দিয়ে বললেন, “ভোবার জন্য রেখে দেবেন। যদি একদিন আসে…”
পরদিন ভোরে সুবর্ণা চিরঘুমে চলে গেলেন।
মাসখানেক পরে অভিমন্যু এল। বাড়ির উঠোনে ফাটল, কাঁথার রোদ নেই, গন্ধ নেই।
পুরনো কাঠের আলমারিতে একটা মাটির হাঁড়ির ভিতর খুঁজে পেল সেই চিঠি—
মায়ের হাতের লেখা, মা-র ভাষায়—
“ভোবা, তুই এখন বড় হইছিস। তোর ভাষাও বড় হইছে।
আমি পুরনো হইয়া গেছি, তোকে আর ডাকি না।
তোর নাম নাকি এখন অভিমন্যু বাবু।
কিন্তু আমি তোকে ‘ভোবা’ বলেই ডাকব যতদিন থাকি।
যেদিন আর থাকব না, তখন তোকে আর কেউ এই ভাষায় ডাকবে না।
ভাষা ফুরায়, মানুষ যায়—
কিন্তু মনে রইয়া যায় সেই ডাক,
যেটা কেবল মায়ের মুখেই ছিল।”
চিঠিটা পড়তে পড়তে অভিমন্যুর বুক ভেঙে এল।
কতদিন কেউ তাকে “ভোবা” বলে ডাকে না। এখন সে শুধু “স্যার”, “বাবা”, “বস”, “ড্যাড”…
আজ অভিমন্যু একটি গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তুলেছে বর্ধমানেই—নাম দিয়েছে “ভোবার ভাষা”।
সেখানে সংগ্রহ হয় বাংলার বিভিন্ন মায়েদের মুখে মুখে থাকা হারিয়ে-যাওয়া উপভাষা, লোকবলির টান, পাড়ার ডাকনাম, এবং সেই পুরনো ছায়া—যেটা বইয়ে নেই, অভিধানে নেই, শুধু হৃদয়ের মাটিতে লেখা।
অভিমন্যু বলে—
“ভাষা শুধু যোগাযোগ নয়, ভাষা হল স্মৃতি।
যে ভাষা মায়ের ছিল, সেটাই পৃথিবীর প্রথম শব্দ।
সেই শব্দ যখন হারিয়ে যায়, একটা জাতি নিজের শিকড় হারায়।
আর আমি? আমি শুধু আমার মায়ের মুখের ভাষাটা ধরে রাখতে চাই—
কারণ ওটাই ছিল আমার পৃথিবী।”